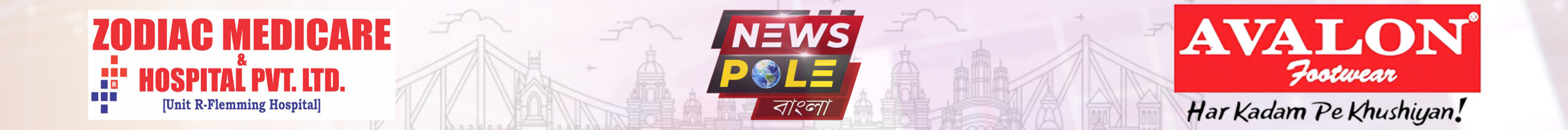বিশ্বদীপ ব্যানার্জি: ভাষার জন্য জীবন দিতে পারে কেউ? দেওয়া সম্ভব? ভাষার জন্য জীবন দিতে পারে কেবল বাঙালিই। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day)। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাকে সম্মান জানানোর দিন। কিন্তু দিনটা এসেছিল বাংলা ভাষার কারণেই। চলুন, ডুব দেওয়া যাক, সে ইতিহাসে।
সাল ১৯০৫। বড়লাট লর্ড কার্জন তথা ব্রিটিশ শাসকের মাস্টারপ্ল্যানে সোনার বাংলা ভেঙে দু টুকরো— “বঙ্গভঙ্গ”! প্রতিবাদে কেবলমাত্র বাংলাই নয়, জ্বলছে গোটা ভারতবর্ষ। এমনই উত্তাল এক সময়ে রবি ঠাকুরের এই গান দেখালো নতুন পথের দিশা। হরতাল এবং ‘অরন্ধন দিবস’ পালনের সাথে সাথে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বঙ্গসন্তানের হাতে রাখী বেঁধে দিয়ে কবি সূচনা করলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী “বয়কট” (বিলিতি পণ্য বর্জন) ও “স্বদেশী” (দেশজ শিল্পের বিকাশ) আন্দোলনের। লিখলেন, “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।…”
আরও পড়ুনঃ Facebook Update: নির্দিষ্ট সময়ের পর লাইভ মুছে দেবে মেটা
অজুহাতটা অবশ্য ভালই সাজিয়েছিলেন কার্জন সাহেব। বলেছিলেন, মাত্র একজন শাসকের পক্ষে এই সুবিশাল বঙ্গদেশের দায়িত্ব সামলানো বড়োই পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আপাত দৃষ্টিতে নিতান্তই নিরীহ অথচ ন্যায়সঙ্গত (অন্তত শাসক আর তার চাটুকারদের কাছে তো বটেই) যুক্তি। কিন্তু ওই যে বললাম, অজুহাত— আসলে পুরোটাই তো ভাঁওতা! একটা জিনিস ইংরেজ সরকার খুব ভালোই জানত যে, বৈপ্লবিক সংগ্রামে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐক্য কেবল বাংলা বা পূর্বাঞ্চল নয়, সমগ্র দেশেরই চালিকাশক্তি। সুতরাং, যেনতেন প্রকারেণ এই সংস্কৃতিতে ফাটল ধরাতে না পারলে কি আর তাদের ভাত হজম হয়?
সাধারণ মানুষ যদিও এসমস্ত প্যাঁচঘোঁচ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। মাতৃসমা সোনার বাংলাকে বৈদেশিক শত্রু দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে!— মোটিভেশনের জন্য তাদের পক্ষে এই যথেষ্ট ছিল। সে যাক, এ নিয়ে নাহয় আরেকদিন বসা যাবে। এখন মূল বক্তব্যে আসি। বিংশ শতকের গোড়ায় বিদেশি সরকার যেই সারকথাটা বুঝতে পেরেছিল, দীর্ঘ প্রায় ৪ যুগ পর বলতে গেলে একরকম জাতভাই খানসেনাদের সেটা মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তা তো আর হতে পারে না।
কথা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশের। ভৌগোলিক অবস্থান সংক্রান্ত জটিলতা অর্থাৎ দুই পাকিস্তানের মাঝে ভারত অবস্থান করার কারণে পূর্বপ্রান্তের ওপর এমনিতেই ক্রমশ রাশ আলগা হচ্ছিল জিন্নার দেশের। তাছাড়া, বাঙালী চাইলে যেকোন দিন ‘লাল কার্ড’ দেখিয়ে দিতে পারে, এ ভয় তো তাদের ৪৭ -এ সেই দেশভাগের সময় থেকেই ছিল। কারণটা আর কিছুই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠতা। হ্যাঁ, প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বঙ্গীয় নরনারী এই সময়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব পান। এরপর ১৯৫২ সালের সুমারী অনুযায়ী পূর্ব-পশ্চিম মিলিয়ে সমগ্র পাকভূমির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ ভাগই ছিল বঙ্গভাষী। এ হেন পরিস্থিতিতে, বলাই বাহুল্য, উর্দুকে রাষ্ট্রীয় তথা সমগ্র দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যমগুলির একমাত্র ভাষার মর্যাদা প্রদান ব্যতীত কর্তৃত্ব স্থাপনের অন্য কোনো বিকল্পই সরকারের হাতে ছিল না।
কিন্তু কালটা হল তাতেই। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে জনগণের চাপে উর্দুভাষী শাসক প্রথমে রফাতেই আসতে চেয়েছিল। বিখ্যাত ইসলামী সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘তমদ্দুন মজলিসে’র প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাসেমের নেতৃত্বে বাঙালী ছাত্রসমাজ ঢাকায় একটি প্রতিবাদ র্যালি বের করলে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম সরকারি ভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার প্রধান মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত নেওয়া হয়। কিন্তু গোটা ব্যাপারটিই ছিল একটি আইওয়াশ। অনেকটা ঠিক মাউন্টব্যাটেন-র্যাডক্লিফের যৌথ উদ্যোগে দেশভাগের অ্যানাসথেসিয়াস্বরূপ ভারতের স্বাধীনতা লাভের মত। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে লিয়াকত আলি খানের সরকার অচিরেই পি.পি.এস.সি (পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন) দ্বারা অনুমোদিত বিষয়-তালিকা থেকে বাংলাকে বাতিল করে দেয়। একই সাথে স্ট্যাম্প এবং মুদ্রাতেও বাংলা শব্দ মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্যস! এরপর আর জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখা যায়নি।
১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবিতে যে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল, ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি (পরবর্তীতে International Mother Language Day) সেটিই দেখা দেয় একটি বৃহৎ গণঅভ্যুত্থান রূপে। উর্দুকেই দেশের একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণার প্রতিবাদে রফিক, সালাম, জব্বার, বরকতদের মতো তরুণ তুর্কিরা সেদিন নিজেদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত অর্পণ করে দেন। আহত হয় বহু নিরীহ মানুষ।
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে আইনসভাতেও। মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, শরফুদ্দীন আহমেদের মতো শাসক দলের সদস্যের সমর্থনে শামসুদ্দিন আহমেদ এবং মনোরঞ্জন ধর সহ মোট ছয় বিধায়ক প্রতিবাদস্বরূপ গণপরিষদ মুলতুবি রাখার দাবি জানান। সাথে সাথে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে আহত ছাত্রদের হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার ও দাবি জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু খুব বেশিদিন সরকার দমননীতির মাধ্যমে নিজেদের অনৈতিক সিদ্ধান্ত অটল রাখতে পারেনি। গণ আন্দোলনে আইনসভার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই তাদের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৭ মে এল সেই শুভলগন। গণপরিষদে মুসলিম লীগের সমর্থনে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রভাষার তকমা লাভ করল বাংলা। রফিক-বরকত-সালামদের প্রাণের ভাষা। এরপর ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে দেশের দ্বিতীয় জাতীয় ভাষার মর্যাদাও প্রদান করা হয়।
মৃত্যুর আগে প্রতিটি জীবকেই ঈশ্বর কোনো না কোনোভাবে জানান দেন— দেহ নইলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে কোনো না কোনো লক্ষণ ফুটে ওঠে। ভাষা আন্দোলনে জনগণের কাছে নতিস্বীকার উর্দুভাষী শাসকের জন্য প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুর প্রথম ঘন্টা ব্যতীত আর কিচ্ছু ছিল না। আগেই বলেছি, বাঙালীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পাক সরকার চিরকালই আশঙ্কার চোখে দেখেছে। ভাষা আন্দোলন এই আশঙ্কাকেই বাস্তব রূপ দিয়েছিল। আর এরপর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে তো পায়ের তলা থেকে তাদের মাটিই সরে যায়।
উল্টোদিকে, নিছক সাফল্যই নয়, বঙ্গসন্তানদের কাছে এ ছিল এক পরম অনুপ্রেরণার অধ্যায়। প্রথমবার তারা উপলব্ধি করে— চাইলে শাসককেও পদানত করা সম্ভব। তাছাড়া, সরকার যে তাদের সমীহ করে, সময়ের সাথে সাথে এ উপলব্ধি ও বাঙালীর মনে গড়ে ওঠে। যে সমস্ত কিছুরই ফল ছিল ১৯৭০ -র নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এবং মুক্তিযুদ্ধের ব্রত। তা যাই হোক, মোদ্দা কথাটা হল— ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (International Mother Language Day) যে চারাটি রোপণ করা হয়েছিল, ১৯৭১ র ২৬ শে মার্চ সেটিই আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলাদেশ নামক এক স্বাধীন মহীরুহ রূপে।